উপন্যাস : শেষের কবিতা
লেখিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ্রন্থ : শেষের কবিতা
প্রকাশকাল : ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
রচনাকাল :
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা “শেষের কবিতা” গ্রন্থটিকে অনেকেই মনে করেন এটি একটি কাব্যগ্রন্থ। মূলত এটি বিশ্বকবির রচিত বিখ্যাত একটি উপন্যাস। যার অমিত ও লাবন্য নামের চরিত্র দুটিও বিখ্যাত। এই উপন্যাসটি প্রথমে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ভাদ্র-চৈত্র অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যা পরবর্তী বছর ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশণী।‘কবিয়াল’ পাঠকদের জন্য রবীঠাকুরের বিখ্যাত এই উপন্যাসটি পর্ব আকারেই প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের জন্য “শেষের কবিতা”কে সতেরোটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে প্রকাশ করা হলো।
 |
| শেষের কবিতা || রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
1111111111111111111111
৮ম পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক/ট্যাপ করুন
শেষের কবিতা || রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পর্ব - ০৯)
বাসা-বদল
গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল, অমিত দিন পনেরোর মধ্যে কোলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু মাস যায়, ফেরার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে, রংপুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক খোঁজ করে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর, তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জানলা-দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্যের সঙ্গে অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।
পরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন। বললেন, 'বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেছে?'
অমিত উত্তর করলে, ‘উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাস্বাবের তপস্যা, খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা। এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছতে পারেন, অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।
অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে, কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো— থেমে গেলেন। ভাবলেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলছেন, তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার 'পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাবণ্যকে বার বার বললেন, ‘মা। লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ কোরো না।'
একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নীচে কম্বল পেতে অমিত একলা বসে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নীচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চলল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কোলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো একদিন সংকল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে পড়ে।
যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন, 'একি কাণ্ড অমিত!'
অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'আমার ঘরটা আজ অসম্বদ্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।'
‘অসম্বদ্ধ প্রলাপ!'
‘অর্থাৎ বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারি দিকে এলোমেলো অশ্রুবর্ষণ হতে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে, তবে সোঁ সোঁ করে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রটেস্ট-স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি— ঘরের মিস্গভর্নমেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্সের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।'
‘মূলনীতিটা কী শুনি।'
‘সেটা হচ্ছে এই যে, যে ঘরওয়ালা ঘরে বাস করে না সে যত বড়ো ক্ষমতাশালীই হোক, তার শাসনের চেয়ে যে দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।'
আজ লাবণ্যর 'পরে যোগমায়ার খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর করে স্নেহ করছেন ততই মনে মনে তার মূর্তিটা খুব উঁচু করেই গড়ে তুলছেন।— 'এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন! গুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি! আর, যদি চেহারার কথা বল, আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে! সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে! খামকা বলে বসলেন কিনা বিয়ে করবেন না। যেন কোন্ রাজরাজেশ্বরী! ধনুক-ভাঙা পণ! এত অহংকার সইবে কেন! পোড়ারমুখীকে যে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে।'
একবার যোগমায়া ভাবলেন, অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁঁদের বাড়িতে। তার পরে কী ভেবে বললেন, ‘একটু বোসো বাবা, আমি এখনই আসছি।'
বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল লাবণ্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির ‘মা’ বলে গল্পের বই পড়ছে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে মনে রাগ আরো বেড়ে উঠল।
বললেন, 'চলো, একটু বেড়িয়ে আসবে।' সে বললে, ‘কর্তামা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।'
যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত দুপুরবেলা খাওয়ার পর থেকেই, তার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল কখন আসবে অমিত। কেবলই মন বলেছে, এল বুঝি। বাইরে দম্কা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছটফট করে। আর, দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝর্নাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাবণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল— যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি, জম্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হু হু করে কী যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায়-আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাবণ্যর কথা— অমনি মস্ত করে, স্তব্ধ হয়ে, অমনি উদার মনোেযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডবনৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে, শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটি অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখির মতো, কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে— সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এত দিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি— আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণ্য আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল ‘সত্য সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই'!
সময় চলে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টন টন করতে লাগল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেললে নিবিড় একটা নৈরাশ্যে; মনে হল ওর জীবনে যা জ্বলবার তা একবার মাত্র দপ্ ক'রে জ্বলে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে; তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি।
এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন বেড়াতে যেতে। ওর উৎসাহ হল না।
যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাবণ্যর সামনে বসলেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বললেন, 'সত্যি করে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাস?' লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, ‘এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কর্তামা?’
‘যদি না ভালোবাস ওকে স্পষ্ট করেই বলো-না কেন। নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেখো না।’
লাবণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।
‘এইমাত্র যে দশা ওর দেখে এলুম, বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও পড়ে আছে! ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কত বড়ো ভাগ্যবতী তা কী এতটুও বুঝতে পার না?’
চেষ্টা করে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য বলে উঠল, ‘আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ কর্তামা? আমি তো ভেবে পাই নে, আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব? আর কেউ কি এমন করে জেনেছে?’
যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এত বড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল! তাকে আস্তে আস্তে বললেন, ‘মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে; সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও— একটুও ভয় কোরো না। যে আলো তোমার মধ্যে জ্বলছে সে আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তা হলে তার কোনো অভাব থাকত না। চলো মা, এখনই চলো আমার সঙ্গে।’
দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।
আপনার পছন্দের গল্পের নাম কমেন্টে জানান
সবার আগে সব পর্ব পেতে যুক্ত হন আমাদের ফেসবুক পেজে।
চলবে ...
১০ম পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক/ট্যাপ করুন
লেখক সংক্ষেপ:
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার এক ধনাঢ্য ও সংস্কৃতিবান ব্রাহ্ম পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৬১ সালের ৭ই মে (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে একজন অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব, কবিগুরু ও বিশ্বকবি অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে।রবীন্দ্রনাথের ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস ও ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন তাঁর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বমোট ৯৫টি ছোটগল্পও ১৯১৫টি গান[ যথাক্রমে গল্পগুচ্ছ ও গীতবিতানসংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
কবিয়াল
কবিয়াল’এ প্রকাশিত প্রতিটি লেখা ও লেখার বিষয়বস্তু, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্যসমুহ সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব। প্রকাশিত সকল লেখার বিষয়বস্তু ও মতামত কবিয়াল’র সম্পাদকীয় নীতির সাথে সম্পুর্নভাবে মিলে যাবে এমন নয়। লেখকের কোনো লেখার বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের যথার্থতার আইনগত বা অন্যকোনো দায় কবিয়াল কর্তৃপক্ষ বহন করতে বাধ্য নয়। কবিয়াল’এ প্রকাশিত কোনো লেখা বিনা অনুমতিতে অন্য কোথাও প্রকাশ কপিরাইট আইনের লংঘন বলে গণ্য হবে।
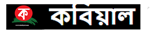
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন