উপন্যাস : শরম
লেখিকা : তসলিমা নাসরিন
গ্রন্থ : শরম
প্রকাশকাল :
জনপ্রিয় লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বহুল আলোচিত উপন্যাস 'লজ্জা'। ১৯৯৩ সালে এটি বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের প্রথম ছয় মাসেই বইটি পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি বৈধ কপি বিক্রি হয়। এরপর ধর্মীয় মৌলিবাদিদের একতরফা বিতর্কের মুখে উপন্যাসটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তৎকালিন বাংলাদেশ সরকার। পরবর্তীতে 'লজ্জা' উপন্যাসটি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি লেখার কারণে দেশ ছাড়তে হয়েছিল লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে।পরবর্তীতে 'লজ্জা' উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দেখা হয়েছিলো লেখিকা তসলিমা নাসরিনের। সেই অনুভূতিকে পুজি করে তিনি লিখলেন নতুন উপন্যাস 'শরম'। এ উপন্যাসটি কবিয়াল পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো।
 |
| শরম || তসলিমা নাসরিন |
11111111111111111111111111111
১৬ তম পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক/ট্যাপ করুন
শরম || তসলিমা নাসরিন (পর্ব - ১৭)
কিন্তু কেউ তখনও জানতো না যে রাতে রাতে মায়ার শরীরে হাত দিত ওই শংকর ঘোষ। মায়ার মুখটা চেপে ধরে রাখতো এক হাতে। এর পর থেকে আর চেপেও রাখতে হয়নি মুখ। মায়া নিজেই কোনও টু শব্দ করতো না। শব্দ করলে যদি ওই রাতেই, বা পরদিন সকাল হওয়ার আগেই তাদের তাড়িয়ে দেয়! তাড়িয়ে দিলে যদি রেললাইন ছাড়া আর কোনও জায়গা না থাকে তাদের থাকার! রেললাইনের কথা মনে হলেই মায়ার কেবল মনে হয় গায়ের ওপর দিয়ে ভয়ংকর দানবের মতো একটা অন্ধ রেলগাড়ি চলে যাচ্ছে। তার শরীর থেঁতলে যাচ্ছে, মাংস-রক্ত ছিটকে ছিটকে পড়ছে তার বাবা-মা, তার দাদার শরীরে। ভয়ে নীল হয়ে থাকতো মায়া। শরীরটাকে মুসলমান শয়তানগুলো খাবলে খেয়েছে। সে তো মরেই গিয়েছিল। দুর্ঘটনাক্রমে বেঁচেছে। এখন কোনও এক হিন্দুর যদি এই শরীরটার দরকার হয় তার পরিবারটাকে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই দিতে আর দুবেলা ভাত দিতে, তবে কী এমন হীরের টুকরো কুমারী শরীর এটি, যে মায়া আগলে রাখবে? সে বাধা দেয়নি। সুরঞ্জন আশঙ্কা করতো কিছু একটা হচ্ছে, কিছু একটা হচ্ছে মায়ার ওপর এবং মায়া বাধা দিচ্ছে না। কিরণময়ীও সম্ভবত বুঝতেন। মায়া যখন কথা বলতো মা আর দাদার সঙ্গে, চোখের দিকে তাকাতো না। অস্বাভাবিক দেখাতো তার আচরণ। কখনও কখনও মায়ার চোখের কোল কালো হয়ে থাকতো, কখনও ঠোঁট ফুলে থাকতো, কখনও গলায় লাল দাগ, আঁচড়ের দাগ গলাযর নিচে। জিজ্ঞেস করলে বলতো, তা জেনে তোমাদের কাজ কী। সেই বলায় একটা অভিমান বা রাগ কিছু একটা থাকতো। কার জন্য, কেন, তা কেউ সঠিক করে বুঝতো না। বুঝতো না, নাকি বুঝতে চাইতো না? আসলে অস্তিত্ত্বের ওই সংকটকালে পাওয়ার মতো যেমন কিছু ছিল না তাদের চাওয়ার মতোও কিছু ছিল না। তখন সুধাময়ের কী করে নতুন জায়গায় ডাক্তারি হবে, কী করে সুরঞ্জনের একটা চাকরি হবে, কেউ জানে না। সাহায্য করার কোনও প্রাণী ছিল না। সুরঞ্জনের সেই শক্তি ছিল না যে মায়াকে জিজ্ঞেস করে এবং উত্তরটা শোনে। উত্তর শুনলে একটা দায়িত্ব থাকে। এই নরক থেকে সবাইকে বের করার দায়িত্ব।
মায়া বলতো, দাদা তোমার একটা চাকরি হবে না? পেতে কি পারো না একটা চাকরি? যদি না পারো তাহলে বলো আমি বেরোই, পথে পথে কিছু খুঁজি। আমার চেয়ে বেশি তো তোমার চাকরি পাওয়ার ক্ষমতা। আমার জন্য কিছু টিউশনির ব্যবস্থা করে দাও অন্তত। নিজেদের জন্য একটা বাসা ভাড়া কি করতে পারছো না?- বেরোচ্ছি তো প্রতিদিন। কিন্তু তো পাচ্ছি না। - মিথ্যে কথা। যে রকম করে খুঁজলে পাওয়া যায়, তেমন করে খুঁজছ না।
মায়ার চোখে সুরঞ্জনের প্রতি কাতর কোন অনুনয় ছিল না, ছিল ঘৃণা। চোখ থেকে বাবা-মার দিকেও ঠিকরে বেরোতো ঘৃণা। অসহায়তা যে কোনও পরিবারকে এমন বীভৎসভাবে গিলে খেতে পারে, পরিবারের কেউ জানতো না। সবাই যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। সুরঞ্জন, অপদার্থ দাদা, কিছুই করতে পারেনি। সুধাময়কেই দিন-রাত পাঁচ-ছ টাকার ডাক্তারি করতে হয়েছে। মায়াকেই বেরিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে টিউশনি জোগাড় করতে হয়েছে। একেবারে বাচ্চাদের পড়ানোর কাজ। পড়ার বইপত্র, পড়ানোর কায়দা, সবই তো আলাদা। বাংলাদেশ থেকে সবে এসেই এখানে একটা কাজ, বিশেষ করে টিউশনির কাজ নেওয়া সম্ভব না। গেছে পড়ানোর কাজ পেতে, পেল বাচ্চাদের গায়ে তেল মালিশ করে স্নান করিয়ে দেওয়া আর বাচ্চার কাপড়চোপড় ধুয়ে দেওয়ার কাজ। বাড়িতে সে বলতো বাচ্চা পড়ানোর কাজ। অত করে মাসে তিনশ টাকা পেত। মায়া যখন বাড়ি ফিরতো সন্ধ্যেয়, দেখতো মেয়েরা সেজেগুঁজে রাস্তায় দাঁড়ায়। প্রথমে না বুঝলেও পরে বুঝতে পেরেছে, টাকা দিয়ে ওদের শরীর কেনে পুরুষেরা। একটা মেয়ের কাছে থেমে মায়া একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কত পাও তোমরা?
মেয়েটি হেসে হাতের আঙুলগুলো মেলে ধরেছিলে। এর ঠিক কী উত্তর হয়, সে জানে না, পাঁচ টাকা নাকি পঞ্চাশ টাকা, নাকি পাঁচশ টাকা। ওই বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য মায়ার ইচ্ছে হয়েছিল সেও দাঁড়ায়। মাস গেলে তিনশ টাকা আয় হওয়ার চেয়ে এ-ই তো ভালো। শরীর একবার ব্যবহার করে পঞ্চাশ টাকা যদি আয় হয়, ছ বার ব্যবহার করলেই তো তিনশ টাকা। পুরো মাস খাটাখাটনির দরকার কী! মায়ার মাথায় ভাবনাটি ঘুরপাক খেতে থাকে। আর এই শরীরের পবিত্রতা রক্ষার যখন আর দায় নেই, তখন প্রয়োজনে শরীর ব্যবহার করেই নরক থেকে বের হওয়াটাই তো একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অপদার্থ বাপ-দাদার আশায় থেকে তো কোনও লাভ সত্যিকারের নেই।
টাকা সাহায্য পায়নি বলে সুরঞ্জন পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছে। ইমোশনাল ছেলে। বাস্তব বুদ্ধি নেই। মায়াও জানে সেটা। জানে যে দাদার ওপর ভরসা করে লাভ নেই, তার পরও সে ভরসা করে। সুরঞ্জনকে খুব অসহায় লাগে তার। ও যে দাদা, ওর চেয়ে কয়েক বছরের বড়, মনে হয় না। যেন ওর আদরের ছোট ভাই। মায়া চোখের দিকে তাকায় না বটে, কিন্তু টের পায় এক একটি চোখে অনিশ্চয়তা আর আশঙ্কা তিরতির করে কাঁপছে । ওসব চোখ সে দেখতে চায় না।
শংকর ঘোষকে মায়া কোনও একদিন খুন করবে, যেদিন তার পায়ের নিচের মাটিটা শক্ত হবে, এই কথাটা মনে মনে সে নিজেকে অনেকবার বলে। প্রতিদিন বলে। ওই শংকর ঘোষের বাড়ি থেকে শেষ পর্যন্ত যেদিন তারা বেরোয়, সেদিন ভেবেছিল কথাটা বলবে তাকে, বলেনি। কারণ যে বাসাটি ওরা ভাড়া নিয়েছে, তা শংকরের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। প্রফুল্লনগর থেকে নন্দননগর। ভয়ে সে বলেনি, যদি আবার আক্রমণ করে বসে তাদের ওপর। মন্দ লোকের মনে হাজার রকম মন্দ জিনিস থাকে, এ কথা মায়ার কি বোধবুদ্ধি নেই যে জানবে না? কখন ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, কে জানে? কখন সবাইকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। কখন নিজেই চুরি করে চুরির মামলায় ফাঁসিয়ে দেয় সবাইকে। সুরঞ্জন যে করেই হোক চার লাখ টাকা আদায় করতে চেয়েছিল শংকর ঘোষের কাছ থেকে, বলেছিল, ওকে খুন করে ওর রক্ত দিয়ে চান করবো আমি, তবে বাড়ি থেকে বেরোবো। মায়া বলেছিল, খবরদার, ভুলে যা সব। বাঁচতে হলে ভুলে যা দাদা। ভুলে যাওয়ার কথা বলার অর্থ ক্ষমা করা নয়। শংকরকে ক্ষমা করেনি মায়া। সবচেয়ে বেশি ক্ষমা করেনি ঢাকার ওই পাষণ্ডদের। আরেকজনকে মায়া ক্ষমা করেনি, সে তসলিমা নাসরিন। 'লজ্জা' লিখে সর্বনাশ করেছে মায়ার। বিয়ের জন্য যেই আসতো, খবর পেয়ে যেতো যে এই পরিবারের কথাই 'লজ্জা'য় লেখা। মায়াকে তো ধরে নিয়ে গিয়েছিল, মায়াকে তো ওরা ধর্ষণ করেছে। সুতরাং বিয়ে হবে না। মায়ার সঙ্গে কিছু যুবকের আলাপ হয়েছিল, তারা আগ্রহী ছিল প্রেম করতে, বিয়ে করতে, কিন্তু পিছু হটেছিল ওই কানাঘুষায় যে, মেয়ের কুমারীত্ব তো নষ্ট হয়েছে। মেয়েকে মুসলমান ছেলেরা ধর্ষণ করেছে। হিন্দুরা ধর্ষণ করেছে, এটা যত না দুঃসংবাদ, তার চেয়ে বড় দুঃসংবাদ মুসলমানরা ধর্ষণ করেছে। মায়ার বিয়ে হয় না। সে বুঝে যায়, বিয়ে তার হবে না। ওই 'লজ্জা' বইটা যদি না বেরোতো, হত মায়া চিৎকার করে কাঁদে। বাড়িতে যত 'লজ্জা'র কপি ছিল, আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রায় কি উন্মাদের মতো সে হয়ে যায়নি? বিদেশ বিভুইএ নতুন করে জীবন শুরু করার মতো অভিশাপ আর কী আছে! হাতে কোনও টাকা পয়সা না নিয়ে, কারও কোনও সহযোগিতা ছাড়া জীবন শুরু করা যায় না। জীবন বরং শেষ করা যায়। মায়া অনেকবার আত্মহত্যা করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত করেনি।
সংসারে হু হু করে অভাব বাড়ে। আর মায়া ছটফট করে। মায়া শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলো তপন মণ্ডলকে। মাতাল। বেকার। কেউ কেউ বলে ছোট জাত। জাত নিয়ে কিছু যায় আসে না মায়ার। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, সে মুসলমান নয়, সে হিন্দু, এটাই সবচেয়ে বড় খবর। মায়া লুফে নিয়েছিল তপনের প্রস্তাব। বিয়ের পর ঘোমটা মাথায় শ্বশুরবাড়ি উঠেছে। শ্বশুরবাড়ির কুড়ি পঁচিশজনের জন্য রান্না করা, তাদের খাওয়ানো, তাদের ঢেঁকুর তোলানো। দুপুরে ভাত, রাতে রুটি। রাতে নিজের হাতে প্রতিদিন পঞ্চাশটা রুটি বানাতে হয়। বাড়ির কাজে তিন জার সঙ্গে ভাগ হয়েছে বটে, কিন্তু নিজের ভাগে পাহাড় সমান কাজ। মায়া কখনও রান্নাঘরের কাজ করেনি। জানে না সে কী করে করতে হয়। এখন শ্বশুরবাড়িতে, রান্না করতে জানি না, সংসারের কাজকর্ম করিনি আগে, বলে রেহাই পাওয়া যাবে না। মাতাল কখনও বাড়ি ফেরে, কখনও ফেরে না। তাকে আদর আহলাদ দিয়ে পোষে যাদবপুরের এক বয়স্ক মহিলা। টাকা পয়সার অভাব নেই, সেই টাকায় শুয়ে বসে খায় তপন। মহিলার স্বামী নেই, দুটো ছেলেমেয়ের বিদেশে বাস। কলকাতায় একা, সঙ্গী তপন। তপনের মতো মাতাল বেকারই তার দরকার। মদ খাওয়ালেই কুকুরছানার মতো লেজ নেড়ে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করে। বিয়ের পরপরই জা-দের কাছ থেকে সব জেনে গেছে মায়া। অনেক ফেরাতে চেয়েছে তপনকে। মদ ছাড়াতে চেয়েছে, মহিলা ছাড়াতে চেয়েছে, পারেনি। ছাড়াতে চেষ্টা করার সময়ই নিজের শরীর বারবার সে পেতে দিয়েছে, পেতে দেওয়া শরীরের ওপর তপন খেলাচ্ছলে যা করেছে, তাতে দুটো ছেলেমেয়ের জন্মের বীজই রোপন করা হয়েছে, সত্যিকার কাজের কাজ কিছু হয়নি।
তপন ফেরেনি। বিয়ে করতে হয় বলে তাকে করতে হয়েছে। শুতে তার ভালো লাগে বলে শুয়েছে বউএর সঙ্গে। কিন্তু বউ বাচ্চার জন্য কোনও আকর্ষণ জন্মায়নি। বড় পরিবারে বাচ্চারা অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে তরতর করে বড় হয়ে যেতে থাকে। বাবা করে না, বাচ্চাদের খোঁজ খবর করে ঠাকুরদা জ্যাঠামশাইরা। দায়িত্ব মায়ার। একটা ওষুধ কোম্পানিতে সে ঢুকেছিল দেড় হাজার টাকা বেতনে, সাড়ে ছ হাজার টাকা হয়েছে বেড়ে। সংসারে খাবার টাকা দিতে হয় আটশ। বাকিটা ছেলেমেয়ে এবং নিজের কাপড়চোপড়, বিস্কুট চানাচুর, বাসভাড়া মেট্রোভাড়া, ইস্কুল খরচ ইত্যাদিতে চলে যায়। এক পয়সাও কখনও হাতে থাকে না। প্রয়োজনে নিজের মা দাদার কাছে যে হাত পাতবে, সে জো নেই। মায়া তারপরও শ্বশুরবাড়িতে থাকে, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর পরে, হাতে পলা শাঁখা, লোহা। ঘরে ঠাকুর দেবতা। ভীষণ সে কালিভক্ত। সুযোগ পেলেই কালিঘাটে পুজো দেবে, সম্ভব হলে চলে যাবে দক্ষিণেশ্বর। এছাড়া তেমন তার নেই সিনেমা থিয়েটার দেখা বা গানের মেলায় যোগ দেওয়া, বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার শখ। দেশে যা শখ ছিল, বিদেশে এসে সবই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছে অথবা করতে হয়েছে। সত্যি বলতে, মায়ার কোনও বন্ধু নেই। জীবনে স্বামী নামক প্রাণীর অস্তিত্ব নেই, তারপরও সিঁদুর পরে মায়া। কেন পরে! নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেই সে উত্তর দিয়েছে, কারণ আর যেন তাকে সহজলভ্য মেয়ে বলে কেউ না মনে করে। ঘরে বাইরে রাস্তাঘাটে। স্বামী, সংসার, শ্বশুরবাড়ি, সিঁদুর, সন্তান-এগুলো থাকলে সম্ভ্রম থাকে। না থাকলে লোকে ছিঁড়ে খায়। মায়ার কাছে শ্বশুরবাড়ি নরক নয়, বরং বেঁচে থাকার জায়গা। স্বামী কখনও দু সপ্তাহ কখনও মাস গেলে বাড়ি ফেরে। বাড়ির কাছে কয়েকদিন ফুটপাথে মদ খেয়ে পড়ে থাকাকে টেনে বাড়ি ঢুকিয়েছে মায়া। বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছে তার শাড়ি কাপড়। তারপরও মায়া ভাবেনি শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে স্বামী ছেড়ে সে চলে যাবে। কোথায় যাবে, তার তো জায়গা নেই কোথাও! কোথাও গিয়ে আর সে দুর্নাম কামাতে চায় না। আর ঝড়ঝঞ্ঝা চায় না। একটা দশ বাই দশ ফুট ঘরে ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, ওদেরই নিজের দুপাশে নিয়ে মায়া ঘুমোয়। বিছানাতেই খাওয়া, বিছানাতেই লেখাপড়া। বড় খাট পাতলে ঘরে আর তেমন জায়গা কই অন্য জিনিস পাতার! দুটো ছেলেমেয়ে যদি বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তবে যদি এ বাড়ি থেকে বেরোয়, মায়ের দেখাশোনা করে, মাকে শান্তি দেয়, তার ভরসায় মায়া থাকে।
কয়েক মাস পরপর সুরঞ্জনকে একটা সার্ট কিনে দেয় মায়া, কিরণময়ীকে শাড়ি। একটা নতুন সার্ট বোনের কাছ থেকে পেলে তার আনন্দ হয়, কিন্তু বোনকে সে কী দিতে পারে! কিছুই তো না। মায়া কাঁদে, অভিযোগ করে, চিৎকার করে, ক্রোধে ফেটে পড়ে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাকে ভীষণ ভালোবাসে সুরঞ্জন জানে। যে ভালোবাসে সে যতটা জানে তার চেয়েও বেশি জানে যাকে কেউ ভালোবাসে, সে।
কিরণময়ী মাঝে মাঝে যখন দেশের কথা মনে করে চোখের জল ফেলেন মায়ার সহ্য হয় না। ওই দেশের কথা উচ্চারণ করবে না একবারও। ওই দেশই আমাদের সর্বনাশ করেছে। ওই দেশ আমার জীবনের যত স্বপ্ন, যত সম্ভাবনা সব নাশ করে দিয়েছে। কিরণময়ী বরং দেশের কথা সুরঞ্জনকে বলে শান্তি পায়, ছেলে চুপ করে শোনে। বাজার থেকে একটু দেশের এটা, একটু দেশের ওটা কিনে এনে সুরঞ্জনকে রেঁধে খাওয়ায়। বেলঘরিয়ায় ভর্তি ছিল দেশের লোক। পার্ক সার্কাসে এসে অবদি কিরণময়ী কোনও দেশের লোকের সন্ধান পায় না। সবই এদেশি, ঘটি। শ কে স বলে, স কে শ বলে। উত্তর কলকাতার কিছু ছেলে সুরঞ্জনের কাছে আসে। ওদেরও ওই একই অবস্থা। বাশে চড়া যায় না, সসাংকর সাসন চলছে। কিরণময়ী মায়াকে যে দেশের সুখের স্মৃতি নিয়ে দুটো কথা বলবে, সেই সবাই মিলে সুধাময়ের বন্ধুর বাড়িতে চলে গেল পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ঘুরে এলো, মায়া তো ফিরতেই চায়নি, নৌকো করে সবার সুন্দরবন চলে যাওয়া, সেই হাসি খুশির দিন, বৃষ্টি হলেই বাড়িতে খিচুড়ি আর ইলিশ খাওয়ার ধুম, মায়ার সেই পাড়া জুড়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে খেলার সেইসব দিন। দিন তো ওগুলোই মনে করার, সুখ পাওয়ার। দিন কী আর কিছু আছে, যে দিন নিয়ে গোল হয়ে বসে গল্প করবে, মন ভালো হবে। কষ্টের যন্ত্রণার দিনগুলো কিরণময়ী যত পারেন স্মৃতি থেকে সরিয়ে রাখতে চান। মায়া ঠিক উল্টো, মায়া বাংলাদেশের কোনও স্মৃতিই আর মনে করতে পারে না তার ওই অপহরণ আর ভাষায় যা বর্ণনা করা যায় না তাকে ছিঁড়ে কামড়ে একপাল মুসলমানের ধর্ষণ করা। কলকাতার বৃষ্টি কিরণময়ী জানালায় বসে উদাস চোখে দেখে, মায়া নেই ভেজার, সুধাময় নেই পদ্মার ইলিশ কিনে আনার। ইলিশের মতো দামি মাছে কারও হাত দেওয়ার যো নেই। দাম কমলে হয়তো কিরণময়ী কিনে আনে ছোট দেখে ইলিশ। মায়াকে ডেকে খাওয়ায়, মায়া সেই ইলিশ এমনভাবে খায়, যেন শুক্তো খাচ্ছে। ইলিশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পদ্মার নাম, পদ্মার সঙ্গে বাংলাদেশের নাম। মায়ার সয় না এতসব। মায়ের আবদারে অনুরোধে খায় বটে সে, খেয়ে কোনও সুখ পায় না। তবু ইলিশ যে খেতে পাচ্ছে, এ দেখেই সুখে চোখের জল মোছেন কিরণময়ী। সুধাময় থাকলে আজ পরিবারের এমন অবস্থা হত না। ছেলেমেয়েদের মুখে কখনও একটুখানি হাসি ফুটলে কিরণময়ী সুধাময়ের কথা ভেবে চোখের জল ফেলেন। সুধাময় চলে গেছেন আজ অনেকগুলো বছর হয়ে গেল, তবু চোখের কিছু জল তাঁর জন্য তোলা আছে কিরণময়ীর। এত অভাব যায়, তিনি সামলে নেন। যুদ্ধ করার দরকার হলে করেন। একাকীত্বে ভোগেন। অনিশ্চয়তা জোঁকের মতো কামড়ে ধরে রাখে। কিছুতেই চোখের জল ফেলেন না কিরণময়ী। কিন্তু সুরঞ্জন যেদিন জড়িয়ে ধরে বলে, মা তোমাকে দেখো গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি বানিয়ে দেব। তোমাকে নিয়ে পূর্ণিমায় গঙ্গাবক্ষে নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়াবো। বা মায়া যেদিন একটা শাড়ি এনে পরিয়ে দিয়ে বলে, কী সুন্দর লাগছে মাকে, কী সুন্দর আমার মা। তখন সুধাময়ের কথা মনে করে চোখ ভিজে ওঠে কিরণময়ীর। এই সুখের সময়গুলো তিনি দেখে যেতে পারলেন না।
মাঝে মাঝে যখন খুব খাঁ খাঁ লাগে, সুরঞ্জনকে ডেকে কাছে বসিয়ে চুলে আঙুল বুলিয়ে বলেন কিরণময়ী, চল দেশে ফিরে যাই। শুনে সুরঞ্জন কিছু বলে না। নিঃশব্দে উঠে যায়। পিছনে কিরণময়ী মিহি সুরে কাঁদতে থাকেন। পার্ক সার্কাসে আসার পর থেকে মাঝে মাঝে বলছেন কিরণময়ী, যেখানে ছিলাম, সেখানেই চল চলে যাই, এখানে তো ঘর ভাড়াও বেশি। সুরঞ্জন রাজি হয় না। বলে, ওখানে বন্ধু বান্ধবরা সব শত্রু হয়ে গেছে, ওপাড়া না ছাড়লে মুশকিল হত। সুরঞ্জন মিথ্যে বলার ছেলে নয়। কিরণময়ী ছেলেকে বিশ্বাস করেন।
- কেন? শত্রু হবে কেন? কেন শত্রু বানিয়েছিস তুই। এপাড়ায় শত্রু যদি বানাস? এরকম কি এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় দৌড়োবো তোর কারণে?
সুরঞ্জনের সঙ্গে যত সহজে তিনি মনের কথা বলতে পারেন, মায়ার সঙ্গে পারেন না। ভয়ে ভয়েই মায়াকে বলেছিলেন, তসলিমা তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে খুব।
- কোন তসলিমা? তসলিমা কে? মায়া চোখ কুঁচকে তাকায় কিরণময়ীর দিকে।
- তসলিমা নাসরিন।
- কি চায় সে? ওই রাক্ষুসী কী চায়? আরও ক্ষতি করতে চায় আমার? যথেষ্ট হয়নি, হয়নি যথেষ্ট? ওই ডাইনির কথা কী করে জানো তুমি? কী করে জানো ডাইনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?
কিরণময়ী মুখ খোলেন না। সুরঞ্জনের সামনে গিয়ে কোমরে আঁচল গুঁজে দাঁড়ায় মায়া।
- ওই তসলিমা রাক্ষুসীটার সঙ্গে কি তোমাদের কারও কথা হয়েছে? দেখা হয়েছে?
সুরঞ্জন বইএর পাতা ওল্টাচ্ছিল। ওভাবে ওল্টাতে ওল্টাতেই বললো, - হ্যাঁ দেখা হয়েছে।
- কোথায়?
- আমি গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে।
- আর মা? মার সঙ্গে কী করে দেখা হল?
সুরঞ্জন এবার ধমকে উঠলো, - এত জানার কী দরকার তোর? তুই দেখা করবি না, ব্যস, মিটে গেল।
- না, মিটে গেল না। আমি চাই না তোমরা কেউ ওর সঙ্গে কোনওদিন আর কোনও রকম যোগাযোগ রাখো। যদি রাখো.. মায়া ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।
- যদি রাখো .... তবে বুঝবো, আমার ওপর যা ঘটেছে বাংলাদেশে, আমার জীবনটা এই যে নষ্ট হয়ে গেল, সব ... সব তোমরা অ্যাকসেপ্ট করছো। তসলিমাকে অ্যাকসেপ্ট করা মানে আমার দুরবস্থা, আমার হিউমিলিয়েশান, দিনের পর দিন রেইপ, একটা ড্রাংক মাংকি, একটা রাস্কেল ইডিয়টের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা, আমার মৃত্যু, আমার ডেথকে অ্যাকসেপ্ট করা। আর কিছু না।
মায়া মুখে আঁচল চেপে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। পেছনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিরণময়ী, সুরঞ্জন।
চলবে.......
১৮ তম পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক/ট্যাপ করুন
লেখক সংক্ষেপ:
জনপ্রিয় প্রথাবিরোধী লেখিকা তসলিমা নাসরিন ১৯৬২ সালের ২৫ আগষ্ট ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে ময়মনসিংহ রেসিডেন্সিয়াল স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৭৮ সালে আনন্দ মোহন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন তিনি। এরপর ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৮৪ সালে এমবিবিএস পাস করেন। তসলিমা নাসরিন ১৯৯৪ সাল অবদি চিকিৎসক হিসেবে ঢাকা মেডিকেলে কর্মরত ছিলেন।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে লেখালেখি নয়তো চাকুরি ছাড়তে বললে তিনি লেখালেখি ছাড়েন নি। বরং সরকারি চিকিৎসকের চাকুরিটিই ছেড়ে দেন তিনি। তখন এই লেখিকাকে কেন্দ্র করে উগ্র মৌলবাদীদের আন্দোলনে উত্তাল ছিলো পুরো দেশ। বেশ কিছু মামলাও হয়েছিলো তার বিরুদ্ধে। শেষে এককথায় বাধ্য হয়েই দেশত্যাগ করেন নারীমুক্তির অন্যতম অগ্রপথিক তসলিমা নাসরিন। এরপর তিনি নির্বাসিত অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন।
কবিয়াল
কবিয়াল’এ প্রকাশিত প্রতিটি লেখা ও লেখার বিষয়বস্তু, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্যসমুহ সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব। প্রকাশিত সকল লেখার বিষয়বস্তু ও মতামত কবিয়াল’র সম্পাদকীয় নীতির সাথে সম্পুর্নভাবে মিলে যাবে এমন নয়। লেখকের কোনো লেখার বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের যথার্থতার আইনগত বা অন্যকোনো দায় কবিয়াল কর্তৃপক্ষ বহন করতে বাধ্য নয়। কবিয়াল’এ প্রকাশিত কোনো লেখা বিনা অনুমতিতে অন্য কোথাও প্রকাশ কপিরাইট আইনের লংঘন বলে গণ্য হবে।
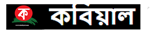
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন